পরিবেশ আইন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (AIRD) লিমিটেড একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির একটি ওয়েব পোর্টাল হলো nDicia (এনডিসিয়া)। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ‘উন্নয়ন আলোচনা’ শীর্ষক আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করে থাকি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নলেজ ডকুমেন্টেশন। আমাদের আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট nDicia-এর ওয়েব পোর্টালে থাকবে এবং সম্পূর্ণ আলোচনাটি nDicia-এর Youtube চ্যানেলে থাকবে। ভবিষ্যতে, এই আলোচনাগুলোকে সম্পাদনা করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হবে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ পরিবেশ আইন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন জনাব শেখ সোহাগ হোসেন, প্রভাষক (আইন) ও সহকারী প্রক্টর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব দেবজ্যোতি সরকার, প্রভাষক, আইন বিভাগ, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, খুলনা। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাসুদ সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্ঠানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ২৬/০৬/২০২৫ তারিখ রাত ০৮:০০ টা থেকে ৯.০০ মিনিট।
মাসুদ সিদ্দিক: ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলুন।
শেখ সোহাগ হোসেন: বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক দুই শতাধিক আইন রয়েছে, যার মধ্যে ১৯৯৫ সালের “বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন” একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে শুরু হয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং কৃষিখাতেও আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়। ফলে পরিবেশের উপর বহুমাত্রিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক চাপও একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ১৯৯২ সালে “Earth Summit” বা “United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)” অনুষ্ঠিত হয়, যা পরিবেশ ও উন্নয়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব আরোপ করে। এর প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের উপরও একটি আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয় পরিবেশ আইন প্রণয়নের জন্য। যদিও স্বাধীনতার পর পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু আইন ছিল, সেগুলো সরাসরি ও কার্যকরভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট ছিল না। তাই, সময়ের দাবি মেনে ১৯৯৫ সালে “বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন” প্রণয়ন করা হয়।
দেবজ্যোতি সরকার: পরিবেশ নীতি মূলত পরিবেশ আইনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ বিষয়ক চাপ এবং দায়িত্ববোধ থেকে বাংলাদেশ প্রথম “জাতীয় পরিবেশ নীতি (National Environment Policy)” প্রণয়ন করে। নীতি এবং আইন—এই দুটি আলাদা হলেও একে অপরের পরিপূরক। আইন হলো বাধ্যতামূলক বিধি, যা অনুসরণ করতেই হবে। অন্যদিকে, নীতি হলো দিকনির্দেশনা, যা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাঠামো তৈরি করে দেয়। পরিবেশ সংরক্ষণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ২০১৮ সালে পরিবেশ নীতিমালা নতুন করে হালনাগাদ করা হয়। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন—জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আইনগত সম্পৃক্ততা, পরিবেশ দূষণ রোধ, এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সমন্বয়, এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা নির্ধারণ। এই নীতিতে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে—কোন মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে, কোন পরিকল্পনা কোন সংস্থা বাস্তবায়ন করবে, এবং জনসম্পদ কীভাবে ব্যবহৃত হবে পরিবেশ রক্ষায়। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ, এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এখনো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নীতি প্রণীত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সফল বাস্তবায়নের জন্য আরো কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।
মাসুদ সিদ্দিক: বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে, পরিবেশ সংরক্ষণ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। আমরা প্রায়ই “Environmental Assessment”, “Environmental Investment” ইত্যাদি শব্দ শুনে থাকি। তাহলে আপনি কি প্রাথমিকভাবে আমাদের একটু ধারণা দিতে পারেন—Environmental Assessment এবং EIA (Environmental Impact Assessment) আসলে কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
শেখ সোহাগ হোসেন: ধন্যবাদ। Environmental Impact Assessment (EIA) একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিরূপণ করা হয়। আমি কিছুক্ষণ আগে যে ১৯৯৫ সালের “বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন” এর কথা বলেছি, সেই আইনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ওই বিধিমালায় বিস্তারিতভাবে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণের ধাপ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রকল্পগুলো ঝুঁকির ভিত্তিতে চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে—Green, Orange-A, Orange-B এবং Red।
- Green Category হলো কম ঝুঁকিপূর্ণ। এর জন্য শুধু একটি সাধারণ ফর্ম পূরণ এবং প্রাথমিক তথ্য প্রদান করলেই পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়া যায়।
- Orange-A হলো মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প, যেখানে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন ও নির্ধারিত ফি জমা দিতে হয়।
- Orange-B ক্যাটাগরিতে কিছুটা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে। এই ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) রিপোর্ট এবং আরও বিশদ তথ্য দাখিল করতে হয়।
- Red Category হচ্ছে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প (যেমন: তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদি) । এসব ক্ষেত্রে EIA বাধ্যতামূলক, এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে Public Consultation গ্রহণ করাও একটি শর্ত।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়াগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। EIA রিপোর্ট প্রায়শই “manipulated” হয় এবং পরিবেশ ছাড়পত্রও দুর্নীতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। বিশেষ করে Red Category প্রকল্পগুলোতে সঠিকভাবে EIA ও Monitoring করা হয় না।
মাসুদ সিদ্দিক: অর্থাৎ দেশে আইন আছে, কিন্তু সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই? পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে, অথচ আইনের প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়।
দেবজ্যোতি সরকার: একদম ঠিক বলেছেন। বাস্তবতা আর নীতিমালার মাঝে এক ধরনের ব্যবধান বিদ্যমান। বাংলাদেশে EIA প্রক্রিয়া অনুসরণ করার কথা থাকলেও অনেক সময় তা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। একটি প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে তার পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করার কথা থাকলেও, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিজেদের সুবিধামতো তথ্য উপস্থাপন করে। তারা নিজেরাই প্রকৃত পরিবেশগত ক্ষতি অনুভব করে না বা করতে চায় না। ফলে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। আরও বড় সমস্যা হলো Monitoring এবং Follow-up Mechanism-এর অভাব। যেমন, রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদাহরণ ধরা যাক—প্রকল্প শুরু হয়েছে, কিন্তু এখন এটি সুন্দরবনের উপর কী প্রভাব ফেলছে, তা পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়নের জন্য কার্যকর কোনো সিস্টেম নেই। পাবলিক কনসালটেশন বা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণও সীমিত। তাদের অভিজ্ঞতা বা মতামত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। এছাড়া দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জটিলতা বড় বাধা। অনেক সময় দেখা যায়, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র জটিল এবং ব্যয়বহুল হওয়ায় ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চান না। আবার অনেকেই জানেনই না কীভাবে আবেদন করতে হয়। আমি মনে করি, যদি পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটালাইজড ও পাবলিকলি এক্সেসযোগ্য করা যেত, তাহলে অনেকটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হতো। সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজ জানতে পারত, কোন প্রকল্পের ছাড়পত্র আছে, আর কার নেই।
মাসুদ সিদ্দিক: আমরা কীভাবে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment – EIA) প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নযোগ্য ও টেকসই করতে পারি? সবাই যাতে আইন মেনে চলে এবং প্রকল্প পর্যায়ে এর যথাযথ প্রয়োগ হয়, তা কীভাবে সম্ভব?
দেবজ্যোতি সরকার: বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে আমরা দেখি, তা অনেক সময় শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন—কীভাবে EIA প্রক্রিয়াকে আমরা টেকসই করতে পারি। আমার মনে হয়, আমাদের মানসিকতার একটি বড় পরিবর্তন দরকার। আমরা, বাঙালিরা অনেক সময়ই কাজকে গাফিলতি করে দেখি—যেমন “কীভাবে যেন ম্যানেজ করে ফেললাম!” এই ভাবনা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা EIA বা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটকে অনেক সময় শুধুই কাগজ হিসেবে দেখি, যার মাধ্যমে শুধু অনুমোদনটা আদায় করলেই হয়—কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়নটা হয় না। আমরা যদি পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের দিকে আরও জোর দিই এবং দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে পারি, তাহলে অনেকটাই পরিবর্তন আনা সম্ভব। পরিবেশ অধিদপ্তরের উচিত নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে যদি ডিজিটালাইজ করা যায়, যেমন বর্তমানে ভূমি কর অনলাইনে দেওয়া যায়, তেমনি প্রতিটি প্রকল্প বা ফ্যাক্টরি যেন তাদের পরিবেশ ছাড়পত্র, রিপোর্ট, এমনকি ভিডিও প্রতিবেদন পর্যন্ত জমা দিতে পারে—এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসনকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় ছোট ছোট প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে, যেগুলোর ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তর বা বন অধিদপ্তর সরাসরি উপস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় স্থানীয় সরকার বা উপজেলা প্রশাসন যদি সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়, তাহলে প্রভাবিত এলাকার মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ অনেকটাই সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।
মাসুদ সিদ্দিক: আপনি যদি সংক্ষেপে বলেন—বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলো কী? যেমন—বায়ু, পানি বা শব্দ দূষণের বিষয়ে কিছু বলবেন?
দেবজ্যোতি সরকার: হ্যাঁ, অবশ্যই। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে প্রধান যে উপাদানগুলো দেখা যায়, তা হলো—
১) বায়ু দূষণ
২) পানি দূষণ
৩) শব্দ দূষণ
৪) প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য দূষণ
বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইটভাটা, কলকারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যেমন—রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ভবিষ্যতে বায়ু দূষণে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।
পানি দূষণের ক্ষেত্রে আমরা বুড়িগঙ্গা নদীর অবস্থা থেকে উদাহরণ নিতে পারি। শিল্পবর্জ্য, ট্যানারির বর্জ্য, ঘরোয়া বর্জ্য ইত্যাদি সরাসরি নদীতে ফেলায় নদী একসময় মৃত্যুপ্রায় হয়ে পড়ে। অথচ এগুলো অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। শব্দ দূষণ এখন শুধু যানবাহন বা কারখানায় সীমিত নেই—বিভিন্ন এলাকা, মাইক, কনস্ট্রাকশন ও এমনকি বিয়েবাড়ির লাইটিং পর্যন্ত আমাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। বর্তমানে এমনকি আলোক দূষণ (Light Pollution) পর্যন্ত আমাদের চোখে-মাথায় প্রভাব ফেলছে—যা আমরা উপলব্ধি করি না, কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—এই সমস্যাগুলো সমাধানের আগে আমাদের নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। “আমি আয় করব, বসে বসে পরিবেশ রক্ষা করব”—এই চেতনা তৈরি করতে না পারলে কোনো নীতিমালাই কার্যকর হবে না।
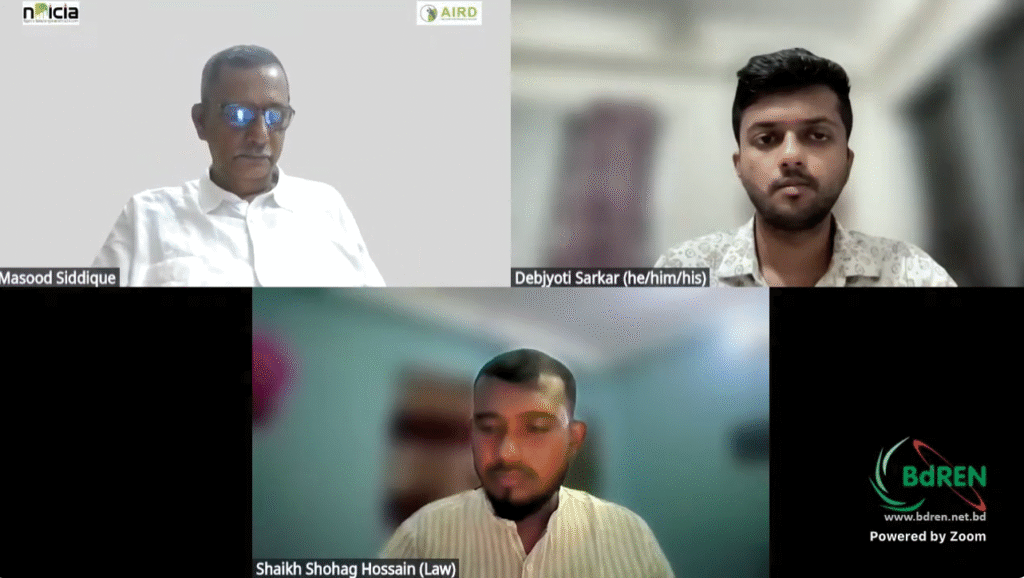
মাসুদ সিদ্দিক: বন উজাড় ও পাহাড় কাটার মতো কাজ পরিবেশের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলছে—দূষণ বাড়ছে, বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কী? পরিবেশ আইন ও বন আইনের মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করা যেতে পারে?
শেখ সোহাগ হোসেন: ১৯২৭ সালের বন আইনটি একটি শতবর্ষ প্রাচীন আইন, যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত হয়। যদিও পরবর্তীতে কিছু সংশোধন হয়েছে, তারপরও এই আইনের অনেক ধারা এখনো কার্যকর রয়েছে। এই আইনে বনভূমিকে রিজার্ভ ফরেস্ট, প্রটেকটেড ফরেস্ট এবং অন্যান্য ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গাছ কাটা, জমি দখল, পাহাড় কাটা, বনাঞ্চল দখল ইত্যাদি বিষয়ে আইনটি সুস্পষ্ট বিধান দেয়। তবে বাস্তবতা হলো, আইন রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগ দুর্বল। অনেক সময় সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বনভূমিকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করলেও, জনগণ সেই তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকে না। ফলে বন উজাড়, অবৈধ বসতি স্থাপন এবং পাহাড় কাটা অব্যাহত থাকে। বন কর্মকর্তারা অনেক সময় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, কেউ কেউ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অবৈধভাবে গাছপালা কাটতে বা সম্পদ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেন। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি—অবৈধভাবে গাছ কাটা, গোলপাতা সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ, এমনকি ইলিগ্যাল ফিশিং-ও চলছে। এই সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে প্রশাসনিক দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার ঘাটতি। যদি এই সমস্যা সমাধান করা যায়, তাহলে আমাদের বনভূমি রক্ষা সম্ভব।
মাসুদ সিদ্দিক: বন ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির সম্পৃক্ততা জরুরি। কিন্তু যেসব মানুষ বন নির্ভর, তাদের পর্যাপ্তভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না বলেই হয়তো এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।এবার দেবজ্যোতি সরকার, আপনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকূল অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে চিংড়ি চাষজনিত পরিবেশ দূষণ ও লবণাক্ততা বাড়ার বিষয়টি নিয়ে বলুন। পরিবেশ আইন দিয়ে কীভাবে এটার মোকাবিলা করা যায়? এটি কি পুরোপুরি রোধ করা উচিত, নাকি কোনো ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সম্ভব?
দেবজ্যোতি সরকার: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি নিজেও উপকূল এলাকার মানুষ এবং বাস্তবতা হলো—চিংড়ি চাষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার কারণে এর সুফল ও কুফল দুটোই আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। চিংড়ি চাষ, বিশেষ করে বাগদা চিংড়ি, লবণাক্ত পানির ওপর নির্ভরশীল। আর এই লবণাক্ত পানিই ধীরে ধীরে আমাদের জীববৈচিত্র্য, মাটি, পানি এবং বসতবাড়ির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেক সময় আমরা দেখি, ইটের বাড়ির গায়ে লবণের আস্তরণ পড়ে যায়; এমনকি পানি এতটাই লবণাক্ত যে খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। চিংড়ি চাষে একসময় অনেকেই আর্থিকভাবে লাভবান হলেও, বর্তমানে মাছের উৎপাদন ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তা কমে গেছে। মানুষ এখনো বুঝতে পারছে না, যে লবণাক্ত পানি জমিতে ঢোকানো মানেই শুধু নিজের ক্ষতি নয়—চারপাশের পরিবেশ ও সমাজের ক্ষতিও নিশ্চিত। এই প্রেক্ষিতে, ২০১৪ সালের জাতীয় চিংড়ি নীতিমালার কথা উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে—চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। যেমন:
- লবণাক্ত পানি যাতে আশপাশে ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য পুকুরের বাঁধ কনক্রিট বা উন্নত উপায়ে নির্মাণ করতে হবে।
- বসতবাড়ির আশপাশে যেন লবণাক্ততা না বাড়ে, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
- চাষাবাদ এমনভাবে করতে হবে যেন স্থানীয় জনগণ, কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
আমার মতে, চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এটি হতে হবে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে। পরিবেশ আইন, বিশেষ করে EIA বা Initial Environmental Examination (IEE) বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, মনিটরিং ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কঠোরতা আনতে হবে।
মাসুদ সিদ্দিক: এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উঠে আসে—আমাদের দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত আইন থাকলেও, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আমরা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাচ্ছি না। উদাহরণস্বরূপ, বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে এখনো বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দূষিত দেশ হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগ স্মার্ট পেট্রোলিং ব্যবস্থা চালু করলেও, পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) এমন কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। বন বিভাগ যদিও স্মার্ট পেট্রোলিং কার্যক্রম চালাচ্ছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে আমরা সেই উদ্যোগ তেমনভাবে লক্ষ্য করছি না। অথচ ECA 1995 ও ECR 1997-এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।পরিবেশ অধিদপ্তরের এই বিষয়ে কী করণীয় এবং তারা কেন পিছিয়ে আছে?
শেখ সোহাগ হোসেন: স্মার্ট পেট্রোলিং বিষয়ে বলার আগে আমি চিংড়ি চাষ প্রসঙ্গে দু’টি কথা বলতে চাই। জনাব দেবজ্যোতি সরকার খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। আমি নিজেও চিংড়ি অঞ্চল থেকে এসেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির বাস্তবতা সম্পর্কে জানি। আমার প্রস্তাব হলো, কৃষিজমি ও চিংড়ি চাষের মধ্যে একটি পরিষ্কার সীমারেখা নির্ধারণ করা দরকার। অনেক কৃষিজমি এখন চিংড়ি খামারে পরিণত হচ্ছে, যার ফলে ঐ অঞ্চলের ধান উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা সংকট দেখা দিতে পারে। কাজেই, চিংড়ি চাষকে নির্ধারিত জোনে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কৃষিজমি রক্ষা করা জরুরি।
এবার আসি স্মার্ট পেট্রোলিং প্রসঙ্গে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা হচ্ছে—পর্যাপ্ত জনবল ও দক্ষতা ঘাটতি।
স্মার্ট পেট্রোলিংয়ের জন্য যে সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল দরকার, তা বর্তমানে অধিদপ্তরের নেই। এ ছাড়া যারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। যদি আমরা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় নিয়মিত পরিবেশগত পেট্রোলিং চালাতে চাই, তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে:
- প্রশিক্ষিত ও কারিগরি দক্ষ জনবল তৈরি
- প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের আধুনিকায়ন (ড্রোন, সেন্সর, পরিবেশ মনিটরিং ডিভাইস ইত্যাদি)
- একটি ইন্টিগ্রেটেড মনিটরিং সিস্টেম, যেখানে বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় থাকবে
বর্তমানে বন বিভাগ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে তাদের জুরিসডিকশনাল ওভারল্যাপিং রয়েছে। তাই, একটি সমন্বিত কাঠামো ও অন্তঃমন্ত্রণালয় কো-অর্ডিনেশন মেকানিজম গঠন করা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা। কারণ, দুর্নীতি, প্রভাবশালী মহলের চাপ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে প্রায়শই বাধাগ্রস্ত করে। স্মার্ট পেট্রোলিং ব্যবস্থা চালু হলেও, যদি সেটি দুর্নীতির বলি হয়, তাহলে এর কোনো সুফল আমরা পাব না। আমাদের উচিত হবে, একটি স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর, জনসম্পৃক্ত এবং জবাবদিহিমূলক পরিবেশ মনিটরিং ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহলেই পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তব অর্থে কার্যকর হবে।
মাসুদ সিদ্দিক: এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উত্থাপন করতে চাই—ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট (পরিবেশ অধিদপ্তর) এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা। বাস্তবতা হলো, অধিদপ্তরটি জনবল ও কারিগরি সক্ষমতার দিক থেকে এখনও অনেক দুর্বল। এই সংস্থা যেভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করছে, সেই অনুযায়ী তাদের কাঠামোগত ও আর্থিক শক্তি আরও বাড়ানো দরকার। এই বিষয়ে, জনাব দেবজ্যোতি সরকার, আপনি কী বলবেন?
দেবজ্যোতি সরকার: ধন্যবাদ। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি মনে করি, সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো অর্থায়ন।
যখনই আমরা কোনও প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিচ্ছি, তখন তাকে সেই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত অর্থ ও লজিস্টিক সাপোর্টও দিতে হবে। বাংলাদেশে অনেক সময় আইন ও নীতিমালা থাকলেও, বাজেট বরাদ্দ না থাকায় বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের বাজেট ও জনবল বাড়ানো, আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ, এবং ফিল্ড পর্যায়ে কাজের সুবিধার্থে স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এছাড়াও, অধিদপ্তর আইন প্রণয়নের কাজ না করলেও, আইন বাস্তবায়নে একটি নিয়ামক সংস্থা হিসেবে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো খুবই জরুরি। তাদের উচিত হবে—নাগরিক সমাজ, স্থানীয় সরকার ও গণমাধ্যমের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে মাঠ পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
মাসুদ সিদ্দিক: স্থানীয় সরকারগুলোর কি ভূমিকা থাকা দরকার? থাকলে কীভাবে?
শেখ সোহাগ হোসেন: জি, অবশ্যই। স্থানীয় সরকারকে উপেক্ষা করা যাবে না। তারা যদি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। স্থানীয় চেয়ারম্যান বা ইউপি সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব মুক্ত রেখে যদি তারা সচেতনভাবে কাজ করেন, তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে নদী, পাহাড়, বন রক্ষা সম্ভব হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক সময় স্থানীয় নেতারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্পে সহযোগিতা করেন। এ কারণে তাদের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব ও জবাবদিহির কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।
মাসুদ সিদ্দিক: সাধারণ নাগরিকদের পরিবেশ সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা—এটা কতটা জরুরি? কিভাবে সম্ভব?
শেখ সোহাগ হোসেন: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এ বলা হয়েছে, নাগরিকদের চারটি মৌলিক দায়িত্ব:
১. সংবিধান ও আইন মেনে চলা
২. শৃঙ্খলা রক্ষা করা
৩. নাগরিক কর্তব্য পালন করা
৪. রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা
পরিবেশ হলো রাষ্ট্রের সম্পদ—অতএব পরিবেশ সংরক্ষণ প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।
কিন্তু বাস্তবে নাগরিকরা শুধু সুবিধা নিতে চান, দায়িত্ব পালনে আগ্রহ দেখান না। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার।
আমার প্রস্তাব:
- পরিবেশ শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- স্কুল-কলেজে বৃক্ষরোপণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে
- শিশুরা যেন ছোটবেলা থেকেই জানে, রাস্তা নোংরা করা, গাছ কাটা, শব্দ দূষণ—এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করে
- এই সচেতনতা আগে অভিভাবকদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ক্যাম্পেইন চালিয়ে সরকার ও সিভিল সোসাইটি মিলে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করতে হবে
এইভাবেই আমরা একটি পরিবেশবান্ধব এবং সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে পারি।
মাসুদ সিদ্দিক: আসলে, যদি আমাদের এই প্রজন্ম সচেতন হয় এবং নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে, তবে এক সময় বাংলাদেশে একটা বড় পরিবর্তন আসবে—এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আমাদের এই আন্দোলনে আমরা সক্রিয় থাকতে চাই, কাজ করে যেতে চাই।
এই প্রেক্ষাপটে আমি জানতে চাই, জনগণকে সচেতন করতে শুধু কারিকুলাম নয়, বরং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যারা নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, তাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই, জনাব দেবজ্যোতি সরকার।
দেবজ্যোতি সরকার: নাগরিক সম্পৃক্ততার পাশাপাশি, আমাদের দেশে বেশ কিছু পরিবেশ-বিষয়ক সংগঠন রয়েছে, যারা সত্যিকার অর্থে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও কার্যকর একটি সংগঠন হচ্ছে বেলা—বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া রয়েছে ওয়াটারকিপার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), এবং আরও অনেক সংগঠন, যারা নদী, বন, পাহাড় ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরাসরি কাজ করে। এই সংগঠনগুলো আইনি সহায়তা প্রদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটা বাস্তব উদাহরণ দিই: যেমন, যখন একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন, তখন অনেক সময় তিনি নিজের পক্ষে কথা বলতে পারেন না। তখন কিছু আইনি ও মানবাধিকার সংগঠন তার পক্ষে দাঁড়ায়, মামলা করে, ন্যায়বিচারের দাবি তোলে। তেমনিভাবে, পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও, সাধারণ মানুষ বা স্থানীয়রা যখন প্রতিবাদ করতে পারে না, তখন এই পরিবেশ সংগঠনগুলো পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (PIL) করে, আদালতের দ্বারস্থ হয়, এবং সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। ওয়াটারকিপার বাংলাদেশ এর উদাহরণ দিই—তারা দেশের বিভিন্ন নদী ও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য কাজ করে থাকে। যখন কোন ফ্যাক্টরি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিবেশ আইন না মেনে বিষাক্ত বর্জ্য নদীতে ফেলছে, তখন তারা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে, আদালতে রিট করে, এবং পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও দক্ষতা বজায় থাকলে, সরকারি পর্যায়ে চাপ তৈরি হবে, এবং পরিবেশ আইন বাস্তবায়ন আরও জোরদার হবে।
মাসুদ সিদ্দিক: আপনাদের দুজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ, সময় দেওয়ার জন্য এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কথা বলার জন্য। আশা করি, এই আলোচনা আমাদের সকলকে ভাবতে এবং কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।






